মাসরুর আরেফিনঃ
বহু বছর পর কারও সাহিত্যে নোবেল বিজয় নিয়ে সত্যিকারের খুশি হলাম। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই নোবেল নিয়ে কোনোভাবেই দ্বিধাহীন ও শর্তহীন উল্লাস করতে পারছিলাম না মনে মনে, মানে যাকে সেলিব্রেট করা বলে। চলতি শতকে নাইপল, কোয়েটজি ও ভার্গাস ঝোসা কথাসাহিত্যে নোবেল পেলে অনেক আনন্দ হয়েছিল মনে, সন্দেহ নেই। তার চেয়ে মাত্রায় কিছুটা কম পুলক বোধ করেছিলাম অ্যালিস মানরো, মোদিয়ানো ও ইশিগুরোর নোবেলপ্রাপ্তিতে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ধরনের নিঃশর্ত আনন্দ দিয়েছিল নব্বইয়ের দশক, তা-ও মোট চারবার, অর্থাৎ অক্তাবিও পাজ, সিমাস হিনি, ডেরেক ওয়ালকট ও গুন্টার গ্রাসের নোবেল পাওয়াতে যেমন করে মনে হয়েছিল যে, ব্রাভো, দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোবেল কমিটি, সেরকম খুশি, কিংবা তার চাইতেও বেশি খুশিতে মন ভরেছে এই ২০১৯ সালে এসে—পিটার হান্টকের নোবেল বিজয়ে।
হান্টকের (বানানটা কোনোভাবেই ড বা দ দিয়ে হবে না, নিশ্চিত এটা ট হবে; বাংলায় শুনলাম একমাত্র মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই নামটা ঠিকভাবে লিখেছেন—হান্টকে) সঙ্গে আমার পরিচয় মাঝ নব্বইয়ে, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার প্রিয় শিক্ষক কায়সার হক একদিন টমাস পিনচন ও স্লটারহাউস ফাইভ-এর লেখক কুর্ট ভোনেগাটের কথাসাহিত্যে নতুন ভাষা সৃষ্টির প্রবণতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে, আমার পিটার হান্টকে পড়া উচিত। সেই বোধহয় প্রথম আমার তাঁর নাম শোনা। আমাদের মতো তথাকথিত সিরিয়াস পাঠকদের ছোট মহলে তখন কাজুও ইশিগুরোর রিমেইনস্ অব দ্য ডে-র জয়জয়কার, আর আমাদের অধিকাংশ আলোচনা ঘুরেফিরে শেষ হচ্ছে ভি. এস. নাইপল, বোরহেস বা টমাস পিনচনে গিয়ে, এরকমই একসময়ে জানলাম পিটার হান্টকে নামের অস্ট্রিয়ান এক ভদ্রলোক জার্মান ভাষায় লিখে কথাসাহিত্যের ভাষা, গদ্য ও গল্প বলার টেকনিকে নতুন বিপ্লব ঘটাচ্ছেন ইউরোপে, এবং আরও জানলাম যে প্রচণ্ড জেদি ও একরোখা, প্রায় আধাপাগল এক মানুষ তিনি। জানলাম টমাস বেরন্হার্ট ও পিটার হান্টকে—এ দুই জার্মান লেখকের লেখা না পড়লে নাকি জানাই যাবে না যে কীভাবে গদ্য টানটান ও সুপাঠ্য হয়েও আলো ফেলতে পারে পাতা-ভরা জঙ্গলের ছায়ার নিচে আর উদ্ভাসিত করতে পারে জঙ্গলের প্রতিটি পাতাকে আলাদা আলাদাভাবে, তাদের গায়ের শিরা-উপশিরাসহ।
তারপর মনে নেই যে ঠিক কবে কখন হান্টকে হাতে নিই। তবে অনুমান করি ২০০২-য়ে প্রথম, অর্থাৎ ডব্লু. জি. সেবাল্ড মারা যাবার পরের বছরে সম্ভবত প্রথমবারের মতো পড়ি বেরনহার্টের ‘উডকাটারস্’ এবং হান্টকের ‘দি গোলিস অ্যাংকজাইটি অ্যাট দি পেনাল্টি কিক’, যে বইটির কথা আলাদা করে বলেছিলেন আমার সেই শিক্ষক। টমাস বেরন্হার্ট ভালো লাগে না পড়া বেশি কষ্ট বলে—গল্পের গতিহীনতা, দুর্বোধ্যতা এবং তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের কারণে। তবে হান্টকে-কে এতো ভালো লেগে যায় যে, এর পরের এই ১৬-১৭ বছরে একটানা হান্টকে পড়তেই থাকি, যেভাবে একবয়সে পড়তাম মিলান কুন্ডেরাকে, গার্সিয়া মার্কেসকে বা ইশিগুরোকে।
হান্টকে অতিপ্রজ লেখক, দুহাতে লিখেছেন কবিতা, নাটক, উপন্যাস। তাঁর কবিতা পড়া হয়নি, তাঁর নাটকের কথা পড়েছি সেবাল্ডের ভ্রমণকাহিনী এবং প্রবন্ধের বই ‘ক্যাম্পো সান্তো’-তে যেখানে পিটার হান্টকের বিখ্যাত নাটক ‘ক্যাসপার’ (১৯৬৭) নিয়ে তাঁর একটা দারুণ প্রবন্ধ আছে ‘স্ট্রেঞ্জনেস, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ক্রাইসিস: অন পিটার হান্টকে’স প্লে ক্যাসপার’—এই নামে, যে প্রবন্ধে সেবাল্ড বলছেন যে, ক্যাসপার ষাট ও সত্তর দশকে ইউরোপে লেখা ও মঞ্চায়িত সেরা নাটক এবং হান্টকের উপন্যাস ‘এ সরো বিয়ন্ড ড্রিমস’ (১৯৭২)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও লিখছেন: ‘সমাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে খারিজ করে দেওয়ার স্ম্ফটিকীভূত চিহ্নটি তখনই ফুটে ওঠে যখন, যেমনটা হান্টকে বলেছেন তার এ সরো বিয়ন্ড ড্রিমস্ উপন্যাসে, “অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রবল প্রয়োজনটা আসে চূড়ান্ত বাকহীনতার হাত ধরেই”।’ অর্থাৎ যখন নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষাটা আপনার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন পড়ে, তখনই দেখা যায় আপনি বোবা, কিছুই বলতে পারছেন না।
ধরা যাক সকালে অফিসে গেছেন, গিয়ে দেখলেন আপনাকে বলা হলো আপনার চাকরিটা আর নেই—কল্পনা করুন এরকম মুহূর্তে কে গিয়ে নিজের বলারটা গুছিয়ে বলতে পারে মানবসম্পদ বিভাগের প্রধানের কাছে? কিংবা ধরা যাক নাইটকোচ চেপে ঢাকা থেকে যশোর যাচ্ছেন, ভোররাতে চলন্ত বাস থামিয়ে দিল একদল ডাকাত, আপনার অনেক কিছু বলার আছে তাদেরকে যে আপনার পকেটের বিশটা হাজার টাকা কতো প্রয়োজনীয় আপনার কাছে, কিন্তু আপনি কোনো কথাই আর গুছিয়ে বলতে পারছেন না। কিংবা, হান্টকে থেকে নিয়েই বলি—তাঁর উপন্যাস রিপিটেশন (১৯৮৬) থেকে—যে, গ্রামের ছেলে আপনি, বড় শহরে এসে দাঁড়াতে চাচ্ছেন নিজের পায়ের ওপরে, রাতে এই বড় শহরের বড়লোকদের সঙ্গে আপনার ডিনার, আপনাকে ওই ডিনারের কথা বলে প্রমাণ করতে হবে যে আপনিও পারেন, কিন্তু তাদের পোশাক-আশাক, জুতোর চকচকানি, হাতের ঘড়ির ঝিলিকের সামনে পড়ে আপনি এতোটাই নিজের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লেন যে গ্রামে যতটুকু কথা বলতেন তার দশভাগের একভাগও বেরুল না আপনার মুখ দিয়ে, এমনকি তারা যখন জোক করছে তখন আপনি অকারণে হাসতে হাসতে ভুলেও গেলেন যে কখন হাসিটা থামাতে হবে। সেবাল্ডের ওই প্রবন্ধ পড়েই সম্ভবত আমার হান্টকে-কে আরও ভালোভাবে জানার তাড়না শুরু হলো।
কী জানলাম? জানলাম হান্টকে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছেন দর্শককে অপমান করার মধ্য দিয়ে। সেই ১৯৬৬-তে তার নাটক ‘ইনসালটিং দি অডিয়েন্স’-এর মঞ্চায়নের মাধ্যমে তিনি শুরু করেছিলেন পাবলিককে গালি দেওয়া—ওই নাটকেই দর্শককে ‘খবিস ইহুদি’, ‘নাৎসি শুয়োর’ ইত্যাদি বলেছিলেন তিনি। অতএব, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর সেই ক্যারিয়ার তিনি শেষ করবেন মানুষের গালি খেয়ে, সবার কাছে অপমানিত হয়ে। ওই নাটক মঞ্চায়নের ৩০ বছর পরে তিনি সার্বিয়ার স্বাধীনতার জন্য পথে নামলেন এবং ভুলেই গেলেন যে সার্বরা কত নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে স্রেব্রেনিকা, বসনিয়া-হার্জেগোভিনায়; উল্টো তিনি সার্বদেরকে তুলনা করলেন নাৎসি নিপীড়নের শিকার অসহায় ইহুদিদের সঙ্গে, অর্থাৎ প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার মুসলিমরাই যেন খুনি, আর খুনিরা যেন সাধু। সার্বিয়ান সরকার হান্টকে-কে একের পর এক সম্মানে ভূষিত করতে লাগলেন এবং কুখ্যাত গণহত্যাকারী স্লোবোদান মিলোসেভিচ মারা গেলে হান্টকে হাজার বিশেক লোকের সামনে মিলোসেভিচের জন্য স্তুতিবাক্য পাঠ করলেন মাইক্রোফোনে মুখ রেখে। অপমানের পাল্লা ঘুরে গেল। সারা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অগণন হান্টকে-পাঠক ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাঁর থেকে। দার্শনিক অ্যালা ফিন্কেলক্রট হান্টকে-কে উপাধি দিলেন ‘আদর্শগতভাবে রাক্ষস’-এর; সালমান রুশদি ১৯৯৯-তে এসে তাকে বললেন ‘বছরের সেরা উন্মাদ (বা আহাম্মক)’; এবং সুসান সন্টাগ ঘোষণা দিলেন যে এ-পৃথিবীর পাঠকেরা আর কখনও হান্টকে হাতে তুলবেন না। অর্থাৎ তুমি যা-ই লেখো না কেন, যা-ই বলো না কেন, জীবনে হয় তুমি লাখ লাখ মানুষের কোনো গণহত্যাকারীর দাফনের দিনে সেখানে হাজির হয়ে শোক করবে, না হয় করবে না—ব্যাপারটা এতটাই সোজা, এখানে অন্য আর কিছু বিচার্য নয়।
আর হান্টকে এসবের মাঝখানে পড়ে কী বুঝলেন? তিনি বুঝলেন যে, সবই তাহলে ভাষার সমস্যা। তাঁর শুরুর দিকের অধিকাংশ উপন্যাসেরই, ‘ক্যাসপার’ নাটকের মতো, অন্যতম প্রধান থিম ভাষা, ভাষার জবরদস্তিমূলক শক্তি, যেখানে ভাষাই এক খেলা, ভাষাই এক অসুখ, ভাষাই এক ওষুধ—কীভাবে আমরা যা বলি তা বলতে চাইনি, কীভাবে জানি যে কী আমরা বলতে যাচ্ছি এবং তা কত বিধ্বংসী হবে, কিন্তু ভাষার জোয়ার মুখে চলে এলে কীভাবে আর থামার জো থাকে না, এবং যে বাকহীন (যেমন ‘ক্যাসপার’ নাটকের ক্যাসপার নিজে) সে যখন কথা বলতে শেখে, নতুন পরিবেশ-পরিমণ্ডলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে সে যখন সমাজের সিঁড়ি ভাঙতে শেখে, তখন কীভাবে তার কথা বলতে না পারার সমস্যার সমাধান হয়ে যায় নতুন এক সমস্যার জন্ম দিয়েই—কথা বলতে পারার সমস্যা। কারণ তার সামনে তখন তারই আগেকার বোবা রূপটা নিয়ে অন্য একজন দাঁড়িয়ে যায় এবার, যে কিনা কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ অবস্থান বদলে যায় মানুষের, নিপীড়ক চলে যায় নিপীড়িতের জায়গায়, নিপীড়িত চলে আসে নিপীড়কের স্থানে, আর এভাবেই চলতে থাকে অনন্তকাল—এক নিষ্ঠুর খেলা।
‘ক্যাসপার’ নাটক নিয়ে হান্টকের নিজের ভাষ্য যে, ওটা ‘স্পিচ টর্চার’। সেই টর্চারটাই তিনি নব্বইয়ে এসে করলেন নিজের ওপরে—খ্যাপামি থেকে। কিসের খ্যাপামি? স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, বসনিয়া-সার্বিয়া যুদ্ধের বা বৃহত্তর বলকান যুদ্ধগুলির যে অফিসিয়াল ‘আমেরিকান ভাষ্য’ বা ‘ন্যাটো জোটের ভাষ্য’ তা অস্বীকার করার, মিডিয়ার এই যুগে মিডিয়া যাকে ‘ন্যায়’ বলে তাকে ‘অন্যায়’ বলার, আর মিডিয়া যাকে ‘অন্যায়’ বলে তাকে ঢালাওভাবে ‘ন্যায়’ বলার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর খ্যাপামি। এরই মধ্যে তাঁর মায়ের আত্মহত্যা তাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে এই পৃথিবীতে কোনো ‘স্থিরতা’ নেই, পৃথিবী পাগলাটে, অস্থির এবং কোনো নিয়ম-না-মানা এক বলগাহীন ঘোড়া, আমরা বাস করছি এক ‘প্যানিক রুমের’ ভেতরে, এবং সেই রুমে চলতে থাকা অশান্তি থেকে জাগা বিরক্তি ও উদ্বেগের একটাই উত্তর: ‘বাথরুমে গিয়ে বসে থাকো’ (উপন্যাস স্লো হোমকামিং, ১৯৭৯)।
এ-উপন্যাসেই হান্টকে লিখছেন: “স্থিরতার ওই জায়গাগুলি খুঁজে বেড়ানোর আমার যে আকাঙ্ক্ষা, সারা জীবন ধরে, পৃথিবীর সবটা জুড়ে আমার যে ওই খোঁজ, প্রায়ই কোনো বিশেষ দরকার ছাড়াই, সেটা কি সম্ভবত আমার মানবসমাজ থেকে পালানোর অভিপ্রায় দিয়ে মোড়া না হলেও অন্তত সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোরই, সমাজ নিয়ে ক্লান্ত হয়ে মুষড়ে পড়ারই এক অভিপ্রায় নয়?” এই উপন্যাসের নায়ক তার নিরাপত্তাহীনতার বোধ থেকে আশ্রয় নেয় বাথরুমে বা পেশাবখানায় গিয়ে—এই বোধ যতটা নিরাপত্তাহীনতার, ততটাই ক্লান্তি ও অবসাদের, অতএব “সে ওখানে গিয়ে বসে থাকে তার কথা বলার ক্ষমতা ফিরে আসার অপেক্ষাতে।” তার প্রয়োজন কথা বলার ‘ইচ্ছেটা ফেরত পাবার’। নায়ক, ব্যক্তিজীবনের হান্টকের মতোই, “তার আত্মার গহিনে মিশে থাকা এই বোবা হয়ে থাকার ব্যাপারটার ভেতরে একটা বিপদ দেখতে পায়—যেন বা সে কোনো একটা জড়বস্তু যার সব শব্দ মরে গেছে চিরতরে, আর সে আকুল হয়ে চাইছে যে কথা বলার কষ্ট ও ভোগান্তিটুকু জীবনে ফেরত আসুক আবার।”
সামাজিক চাপ, সামাজিক একঘেঁয়েমি, একাকিত্ব, অমনোযোগ, ঔদ্ধত্য আর অনিরাপত্তা, এই সবকিছুর সংঘর্ষে প্রায়ই বোবা বনে যায় মানুষ, এবং তখনই “বাথরুমের ভেতরকার স্থিরতা থেকে জন্ম নিতে পারে বিশেষ এক ঘটনার—বলতে চাওয়ার ইচ্ছা।” অন্য কথায়, হান্টকের উপন্যাস ‘স্লো হোমকামিং’ প্রাইভেসি চাইছে এমন এক মানুষের প্রাইভেট কাহিনী, যে-মানুষ নিঃসঙ্গতা আঁকড়ে ধরতে প্রয়াসী, কারণ বাইরে বেশিমাত্রায় হট্টগোল। এ উপন্যাসের অসংখ্য বাথরুমের—একটা হান্টকের গ্রামের বাড়ির দরিদ্র বাথরুম, একটা বার্লিনের, একটা প্যারিসের, একটা জাপানের, একটা বাথরুম চীনের যেখান থেকে দূরে নদী দেখা যায়, এবং একটা এক নামপরিচয়হীন বলকান বাথরুমও আছে বইতে যার ফটোটা তিনি নিজেই তুলেছেন এবং নিজেই বলছেন যে ওটা ‘অদ্ভুত’ এক বাথরুম, ওটা ‘আমাকে কোনোভাবে মানসিক পীড়া দিচ্ছে না, বরং উল্টোটাই’, এবং তারই কয়েক পাতা পরে অন্য কারও তোলা আরেকটা ছবি যাতে দেখা যাচ্ছে বেলগ্রেড থেকে কিছু দূরে বাতায়নিকা শহরে, ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ার ওপরে ক্লিনটনের ন্যাটো বম্বিং চলাকালীন, নিহত হওয়া এক বাচ্চা মেয়ের মৃতদেহ—এরকম অসংখ্য বাথরুম ঘুরে শেষমেশ একটা সত্যই, হান্টকে তা না বললেও, উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোথাও স্থিরতা নেই, বাথরুমগুলিতেও না। সেখানে স্তব্ধতা আছে বটে, বোবার পাথর হওয়ার ব্যাপারটা আছে বটে, কিন্তু মৃতদেহের ছবি তাতে ঢুকে সে জায়গাটাকেও করে তুলেছে অস্থির, সেই আপাতশান্তির বাথরুমে বসেও যারা অনেক কথা বলে তারা চুপ মেরে যাচ্ছে এবং যারা বলে না তারাও কথা বলা শুরু করে যোগ দিতে চাইছে মানবপৃথিবীর উন্মাদনার মধ্যে।
তবে উপন্যাসটা পড়ে আমার একটা কথাই মনে হয়েছিল ওই নিহত মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে। হান্টকে সম্ভবত ওই ছবিটির মাধ্যমেই স্তব্ধ করে দিতে চাইছিলেন তার বিরুদ্ধে ওঠা সব রাজনৈতিক সমালোচনাকে, চাইছিলেন বলতে যে শেষ কথাটা আমারই, তালগাছটা আমারই। কিন্তু শেষ কথা ওটা ছিল না। যতক্ষণ না আমরা জানছি যে ন্যাটো বম্বিংয়ের আগে কতগুলি মুসলিম মেয়ের লাশ ধর্ষণের পরে ওভাবে পড়ে ছিল ওই বাতায়নিকারই রাস্তায়, ততক্ষণ কোনো শেষ কথায় পৌঁছানো যাচ্ছে না এই ভঙ্গুর, দলে-বিভক্ত, ট্রাইবাল মানসিকতায় এবং ধর্মে-বর্ণে-সম্পদে বিভক্ত, এই অস্থির, এই হয় মূক না হয় অতি-বাচাল মানবপৃথিবীতে।
এবার একটু গুছিয়ে কথা বলি। এ-বছরে দু বছরের নোবেল দেওয়া হলো একসঙ্গে। ২০১৮-র জন্য পোলিশ লেখিকা ওলগা তোকারচুক আর ২০১৯-এর জন্য পিটার হান্টকে। দু’জনের নামের সঙ্গেই আসছে ডব্লু. জি. সেবাল্ডের নাম। ঔপন্যাসিক সেবাল্ডকে আমি আমার ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র উৎসর্গ করেছিলাম সেই ২০১২-তে (বোর্হেস ও ব্রুস চ্যাটউইনের পাশাপাশি), এবং সেই উৎসর্গে সেবাল্ডকে ডেকেছিলাম সময়, স্মৃতি আর ক্ষয়ের শিল্পী হিসেবে। আমার নিজের কাছে নিজের হিসাব পরিষ্কার—আমি বোর্হেস ও সেবাল্ডকে মনে করি কথাসাহিত্যের শেষ কথা: বোর্হেস ছোটগল্প ফরম্যাটে এবং সেবাল্ড উপন্যাসে। বহুবার বহু জায়গায় এ-কথা বলেছি, সেবাল্ড নিয়ে লিখেছি, এ-ও বলেছি যে আমার নিজের উপন্যাস ‘আগস্ট আবছায়া’-য় যদি কারও সত্যিকারের প্রভাব থাকে তো সেটা কেবল সেবাল্ডের। এর মানে এটা নয় যে পৃথিবীতে আর কোনো ভালো ঔপন্যাসিক নেই, আর কোনো মাথাঘোরানো রকমের গদ্যশিল্পী নেই, কিংবা আমার কাফকা, চ্যাটউইন, মার্সেল প্রুস্ত, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জোসেফ ব্রডস্কি (প্রবন্ধের বেলায়, তবে সেটাও গদ্যই), জোসেফ কনরাড, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভান তুর্গেনেভ, কালভিনো কিংবা হান্টকে প্রীতি মিথ্যা। আমি বলতে চাই, গদ্য কীভাবে লিখতে হয়, ইতিহাসের সাপেক্ষে সময়ের নানা আঁচড়গুলিকে কী করে বিশ্নেষণ করতে হয়, কোন্ ধরনের অভিঘাত রেখে, কতটা সরব আর কতটা অনুচ্চারিত থেকে, এবং কথাসাহিত্যের কোন্ জায়গাটায় লিরিক্যাল সাবজেকটিভিটি আর কোন্ জায়গায় গিয়ে হিস্টরিক্যাল অবজেকটিভির সব গুলিয়ে ফেললেই বরং সাহিত্যের পাতায় ব্যক্তিমানুষ সত্যিকারের মনে দাগ কাটা কোনো চরিত্র হয়ে উঠতে পারে—কনটেন্টের এই এতগুলি বিষয়, আর অন্যদিকে ফর্মের বিষয় যে উপন্যাস কোন্ ধরনের ফর্ম নিলে অথেন্টিক হয়—প্রথাগত কাহিনী শুরু হলো, মাঝামাঝি পৌঁছাল, শেষ মোচড় দিয়ে শেষ হলো, এই ফর্ম, নাকি উপন্যাসটা হলো প্রবন্ধের মতো, নাকি জার্নাল বা ডায়েরির মতো, নাকি ফটো অ্যালবামের মতো, নাকি সবগুলির মিশেলে নতুন কিছু করার পরীক্ষামূলক ফর্ম—এর সবকিছুর উত্তরই আমি পেয়েছি সেবাল্ডের চারটি উপন্যাস, দুটি সাক্ষাৎকারের বই এবং তিনটে প্রবন্ধের বইয়ে। সেই সেবাল্ডই আবার পিটার হান্টকের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রিটিক এবং তাঁর ওপরে কাফকা ও প্রুস্তের পরে হান্টকের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি।
তো, কম-বলার শিল্পী ও পরোক্ষ উল্লেখের বা দূর উল্লেখের শিল্পী সেবাল্ডের ওপরে এত জোরে বলার বা চিৎকার করে বলার শিল্পী হান্টকের প্রভাব থাকে কী করে? প্রভাবটা গদ্য নির্মাণ রীতির, আর এটাই আসল কথা। আপনি যা-ই লেখেন না কেন, তা কিন্তু ভাষার ওপরে ভর করেই লেখেন, ভাষাই ঠিক করে দেয় আপনার লেখার টোন, শব্দচয়নই চিহ্নিত করে দেয় আপনার মুড, আর শেষমেশ লেখকের মনে দাগ কেটে থাকে ওটুকুই। কী পেলাম এই লেখায়, এর উত্তর সাধারণত আমরা কী গল্প পেলাম তা নয়, এর উত্তর বরং এরকম যে, আমি কী লেখাটা পড়ে এই পৃথিবীতে দ্রুত সরে যেতে থাকা পায়ের নিচের মাটিকে আরও কিছুটা বুঝতে বা ধরতে পারলাম এই পৃথিবীর জল-হাওয়া-রোদ, সুখ-দুঃখ-চাওয়া এবং মৃত্যুর বোধ, এবং জীবনের অ্যাবর্সাডিটি, এবং মনের গভীরে ঘটতে থাকা প্রতিদিনকার নীরব ভাঙচুর, নীরব বিপর্যয়টুকু সহ? কথাসাহিত্য বা কবিতা দিয়ে আমরা পৃথিবীকে নতুন করে, নানা রূপে চিনি, আর ভাষাই ঠিক করে দেয় (যাকে টেকনিক্যালি শব্দশৈলী এবং বাক্য গঠনরীতিও বলা যায়) যে সেই লেখা আমার মনে কী অভিঘাত আনবে—হাসির, বিদ্রোহের, বিমর্ষতার না আত্মোপলব্ধির?
হান্টকে ও সেবাল্ডের মধ্যে কনটেন্টের মিল কম, ফর্মের মিল বেশি। একজন (হান্টকে) একটানে ঝট করে দর্শক ও মঞ্চের অভিনেতাদের মাঝখানের পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলে দেখাতে চান কীভাবে দর্শকও ওই মঞ্চশিল্পীই, মানে যখন মঞ্চশিল্পীরা তাদেরকে দেখছে, আর কীভাবে মঞ্চশিল্পীরা দর্শকদের কাছে দর্শনীয় তো বটেই, তারা তো টাকা দিয়ে টিকিট কেটেই তাদেরকে দেখতে এসেছে, এবং কীভাবে এর ফলে শেষে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহের পুরোটাই একটা নাটক; আর অন্যজন (সেবাল্ড) ওরকম পর্দা ছেঁড়াছেঁড়ির মধ্যে তিনি নেই, তিনি বেসিক্যালি দর্শকসারি বা মঞ্চ, দুটোর কোথায়ও নেই, তিনি আছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে, মঞ্চের পেছনে, আবহসঙ্গীতে, গ্রিনরুমে—গালে হাত দিয়ে দেয়ালের এক ফুটো থেকে কোনাকুনি দেখছেন যে কী চলছে মঞ্চে এখন, আর কীভাবে একজন দর্শক ঘুমে বাঁ দিকে হেলে পড়ছে তো অন্যজন উত্তেজনায় চেপে রেখেছে তার মুঠি। এই দুই দেখার মধ্যেই আবার মিল আছে অনেক, কারণ দুটো দেখার একটাও ব্যক্তির নিজের মনস্তত্ত্বের জায়গা থেকে দেখা হচ্ছে না (যেমন দেখেছেন ফ্লবের বা দস্তয়েভস্কি বা আলব্যের কাম্যু), দুটোই দেখাই দেখা হচ্ছে ইতিহাসের প্রিজমের ভেতর দিয়ে। এটাই হান্টকে ও সেবাল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল—তাদের দুজনেরই নায়ক-নায়িকারা কোনো নিখাদ ব্যক্তিমানুষ নয়, তারা বরং এক নির্দিষ্ট সময়ের ইতিহাসের চাপ-তাপে দগ্ধ বা তাড়িত বা উল্লসিত কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই নিবিড় চিন্তায় মগ্ন, পৃথিবী বিষয়ে আলটিমেটলি হতাশ বা বিরক্ত বা বিব্রত এবং অবধারিতভাবে বিষণ্ণ ব্যক্তিমানুষ, কারণ প্রতিমুহূর্তে তাদের ভেতর ভাঙচুর চলছে ইতিহাসের বিপর্যয়, প্রকৃতির বিপর্যয় ও মৃত্যুর নিশ্চিত কোথায়ও লুকিয়ে থাকা থেকে আসা বিপর্যয়ের বোধ থেকে উদ্ভূত বিপর্যয়—এতগুলি বিপর্যয় নিয়ে।
তো, সেবাল্ড হান্টকে থেকে নিয়েছেন তাঁর গদ্যশৈলী, আর সারা পৃথিবীর অসংখ্য আমার মতো উঠতি লেখক সেবাল্ড থেকে এখন নিচ্ছেন তাদের গদ্যশৈলী, যেমন তোকারচুক। তোকারচুকের ‘ফ্লাইটস’ উপন্যাসটিকে বার বার বলা হচ্ছে সেবাল্ডিয়ান—থিম ও গদ্য, কনটেন্ট ও ফর্ম, দুই বিচারেই। দুর্দান্ত হলুদ রঙ প্রচ্ছদে যে ‘ফ্লাইটস্’-টা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে সেটি খুললেই দেখবেন যে ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকার কোটেশন: “ফ্লাইটস্-এ আছে সেবাল্ড, মিলান কুন্ডেরা, দানিলো কিস—এদের প্রতিধ্বনি”; এবং তারপরে ব্রোকব্যাক মাউন্টেন খ্যাত অ্যানি প্রুর মন্তব্য যে, তোকারচুক সেবাল্ডের সমগোত্রীয়।
আমার পড়া হান্টকের প্রথম উপন্যাসটি (‘গোলিস অ্যাংকজাইটি…’) আমার আজও ভালো লাগে, যদিও ওটা বেশিমাত্রায় অস্তিত্ববাদী, প্রি-ফরম্যাটেড কাম্যু বা আর্নেস্তো সাবাতো। উপন্যাস শুরু হয় পুরো কাফকায়েস্ক ঢঙে: “যখন জোসেফ ব্লখ—এক দালান নির্মাণকর্মী, যে কিনা অনেকদিন আগে ছিল ফুটবলের এক নামকরা গোলকিপার—ওদিন সকালে কাজে যোগ দিতে গেল, তাকে বলা হলো যে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।” এই জোসেফ ব্লখ, যে কিনা পেনাল্টি কিকের সময়ে গোলপোস্টে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে না যে বল ঠিক কোন পাশে আসবে, ডানে বা বামে, এবং সে যখন তার এই না-বোঝা থেকে শেষমেশ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে যায় গোলপোস্টের মাঝখানে, শরীর না-বাম না-ডানে ঝুঁকিয়ে, অর্থাৎ যে খেলোয়াড় কিকটা নিচ্ছে সে কোনোভাবে ধরে উঠতে পারে না যে গোলকিপার ব্লখ কোন্ পাশে ঝাঁপ দেবে, অতএব ক্ষণিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে সে বলটা সোজা পাঠিয়ে দেয় ব্লখের হাতে, জিতে যায় ব্লখ, সাময়িক একবারের নিয়তিনির্ধারিত বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া জেতা, সেই ব্লখ তার এই আচমকা বিজয়ের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না, যেমন সে জানে না যে অস্ট্রিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি কেন সে গলা টিপে খুন করেছে তার সঙ্গে এক রাত কাটানো নিরীহ মেয়েটাকে। সে শুধু বুঝতে পারে যে, তার সমস্যা একটাই: ভাষার সমস্যা; এবং তার কাছে এই ব্যাপারটি ভুতুরে লাগে যে কেউ কীভাবে কথা বলা শুরু করলে আবার একইসঙ্গে জানেও যে বাক্যটি কীভাবে কোন্ ধ্বনি তুলে শেষ হবে; এবং তার বাক্যগুলো কখনও ভালোভাবে বা অর্থ রেখে শেষ হয় না বলেই সে এটাও জানে যে মানুষ তাকে অবিরাম ভুল বোঝে। এই হচ্ছে অবস্থা।
উপন্যাসের শেষে নিজের ভাষা ও শব্দগুলি দিয়ে আর নিজের পৃথিবীকে প্রকাশ করতে পারে না ব্লখ। তখন সে আশ্রয় নেয় সিম্বলের, ছবির, যা উপন্যাসটির একদম শেষ দিকে আছে প্রায় কোয়ার্টার পৃষ্ঠাজুড়ে। আমি ওই সিম্বলগুলির বা চিহ্নগুলির সব কটার অর্থ ধরতে পারিনি; দেখতে কোনোটা মনে হয়েছে কালির দোয়াত, তো কোনোটা কফির শপ, তো কোনোটা একটা বেড়া, একটা পথ, কিন্তু দ্বিতীয় সিম্বলটাকে স্পষ্ট মনে হয়েছে গোলপোস্ট। হান্টকের উপরে লেখা একটা প্রবন্ধের বই আছে, লেখক ডেভিড এন কৌরি, নাম ‘দি ওয়ার্কস অব পিটার হান্টকে’—ইন্টারন্যাশনাল পারসপেকটিভস্ (২০০৭)। সে বইটাও আছে আমার সংগ্রহে, কিন্তু কখনও খুলে দেখা হয়নি, এমনকি ২০১০-এর দিকে যখন আমি একটার পর একটা পিটার হান্টকেই পড়ছি শুধু, সে দিনগুলিতেও না। কেন? ‘গোলিস অ্যাংকজাইটি…’ উপন্যাসে নায়ক ব্লখকে এক অস্ট্রিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসার বলছে: ‘তুমি সব সময়েই আছো এক অসুবিধাজনক অবস্থায়… রিঅ্যাক্ট করা ছাড়া আর কিছুই তো পারো না তুমি।” আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি উপন্যাসের ঠিক ওই জায়গায় ওই বাক্যটা ওভাবে দেখে। বুঝতে পারছিলাম যে ব্লখের সমস্যা তার ভাষার সমস্যা, এবং সেটা কেন, আর বুঝতে চেষ্টা করছিলাম মানুষের মধ্যেকার—ব্যক্তি থেকে সমাজে (ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে নয়)—যোগাযোগের সমস্যা সংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্নগুলি যদি সাইকোলিঙ্গুয়িস্টিকসের প্রশ্নই হয় তো, হান্টকে পড়ার আগে কি আমার ওয়াল্টার বেনজামিন ও হ্বিটগেনস্টাইন পড়া উচিত, সেইসঙ্গে কিছুটা মিশেল ফুকো? এরকম শূন্যতার মধ্যে পড়েই আমি ইচ্ছে করে ডেভিড কৌরির বইটি খুলে কখনও দেখতে চাইনি যে, ‘গোলিস্ অ্যাংকজাইটি…’ উপন্যাসের শেষদিকে ওই সাইনগুলির অর্থ হিসেবে কী অর্থ বোঝানো হচ্ছে পাঠকদের, চাইনি গূঢ় দার্শনিক প্রশ্নের কোনো খেলো বা সস্তা বাস্তবসম্মত অঙ্কমেলানো উত্তর।
সত্যিকার সাহিত্য শেষমেশ গিয়ে সার্থকভাবে একটি সমান্তরাল পৃথিবীই নির্মাণ করে, যা আমাদের পৃথিবীর আয়না হয়েও থাকে স্বতন্ত্র, যা এই পৃথিবী হয়ে উঠতে পারতো কিন্তু হয়নি তেমন এক ‘বিতর্কিত’ পৃথিবী। সে পৃথিবীর নিয়মকানুন, ভাষা, বলা, চলা সব আপনার অপছন্দের হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের তূরীয় মেটাফিজিক্যাল সৃজনক্ষমতার মাপে যদি সব মাপেন—এ কথা মাথায় রেখে যে, কথাসাহিত্যের সেই সমান্তরাল পৃথিবীটা বানিয়েছে মাত্র ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের আজ-বাঁচবে-কাল-মরে-যাবে-মতো একটুখানি মাথার এক মানুষ—তাহলে সম্ভবত হান্টকের লেখায় ডুবে নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি দেখার আনন্দ পেতে পেতে আপনি অগ্রাহ্য করে যাবেন তাঁর ভুল রাজনীতি।
সিরিয়াস পাঠকদের বলব প্রথমেই পড়তে হান্টকের উপন্যাস ‘রিপিটেশান’ (১৯৮৬); তারপর ‘এ সরো বিয়ন্ড ড্রিমস:এ লাইফ স্টোরি’ (১৯৭২); ‘দি স্লো হোমকামিং’ (১৯৭৯); ‘দি মোরাভিয়ান নাইটস’ (২০১৬) এবং ‘শর্ট লেটার, লং ফেয়ারওয়েল’ (১৯৭২; ভিম ভেন্ডার্সের সিনেমা ‘অ্যালিস ইন দি সিটিজ’-এর ছায়া নিয়ে লেখা দুর্দান্ত পথের পাঁচালী বা ভ্রমণ থিমের উপন্যাস, যা কিনা থিম্যাটিক বিচারে ওলগা তোকারচুকের ‘ফ্লাইটস্’-কে জুড়ে দিয়েছে হান্টকের সঙ্গে)।
তো, হান্টকেতে যদি কোনো এই পৃথিবীর সমান্তরালে চলা পূর্ণাঙ্গ নতুন পৃথিবী দেখতে চান তাহলে প্রথমেই পড়ূন তাঁর ‘দি মোরাভিয়ান নাইটস’, যা ব্যাপ্তি ও বিস্ময়ের আলো ছড়িয়ে এক বলকান ইতিহাসে প্রোথিত জাদু ও মায়ার, প্রশ্ন ও সে প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার, কিছুটা নিয়তিনির্ধারিত, কিছুটা মানবসৃষ্ট পৃথিবীর বিচারে গার্সিয়া মার্কেজের ‘হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড’ এর মাকোন্দো-পৃথিবীর সমান।
হান্টকে সম্পর্কে শেষ কথাটি বলি তার বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গবেষক সেই ডব্লু. জি. সেবাল্ডকে উদ্ধৃত করেই। সেবাল্ড বলছেন: “এই বস্তু পৃথিবীর পেছনে কী লুকিয়ে আছে, তা আমাদের মধ্যে যে লেখক দেখার সবচেয়ে বড় সামর্থ্য রাখেন, তিনি পিটার হান্টকে।… পৃথিবীতে তিনি নিজেকে আক্ষরিক অর্থেই মনে করেন স্বাধীন… অতএব কোনো সিদ্ধান্ত ভুল হলো তো ভুল, যিনি আমার বিচার করছেন তিনিও পারফেক্ট নন এবং কোনোকিছুর বিচার আজ এখনই কী করে হয়… শুধু শব্দ দিয়ে তিনি আরও সুন্দর এক পৃথিবীকে আমাদের সামনে দৃশ্যমান করেন… তার রাজনীতি স্পষ্টই ভুল, কিন্তু তিনি শব্দ-বিশ্বকে যা দিয়ে যাচ্ছেন তাকে উপেক্ষা করার পথ কী?”
এই লেখাটা লিখতে লিখতেই বুঝে গেলাম যে, সাহিত্যের জন্য যে লেখকের আছে ফ্রানৎস কাফকার মতো এক্সিস্টেনশিয়ান লেভেলের একাগ্রতা বা নিবেদন, অর্থাৎ না লিখতে পারলে আমার অস্তিত্বই টিকবে না এমন, সেই ৫০ বছর ধরে শিল্পসাহিত্যের নানা মাধ্যমে আলো জ্বালাতে থাকা পিটার হান্টকে লেভেলের এক মহীরুহকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি কী করে সেখানে পারি সেদিনকার ওলগা তোকারচুক নিয়ে কথা বলতে? বড় বেমানান হয়ে যায় সেটা। তাই তোকারচুক প্রসঙ্গে কথা বাড়াচ্ছি না শুধু এটুকু বলা ছাড়া যে, তাঁর ওই ইন্টারন্যাশনাল ম্যান বুকার পুরস্কার পাওয়া ‘ফ্লাইটস্’ উপন্যাসটিই আমি পড়েছি শুধু, মানে যখন তাকে পড়েছে সারাবিশ্ব, একযোগে, এই তো সেদিন। এ ছাড়া তোকারচুকের অন্য কিছু পড়া নেই আমার। তিন মাস আগে পোল্যান্ডের ক্রাকাউতে গিয়ে নিজ চোখে দেখেছি তোকারচুক সে দেশে কত জনপ্রিয় (যদিও জার্মান-বিশ্বের হান্টকের মতো নয় অবশ্যই; হান্টকের যে কোনো বই সাধারণত প্রথম দু সংস্করণের মধ্যেই মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে যায় নির্দি্বধায়)।
সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এটা যে ‘ফ্লাইটস্’ বিস্ময়জাগানো এক সৃষ্টি। ‘ফ্লাইটস্’ আমাদের মতো লেখকদেরকে মনে করিয়ে দেয় সাহিত্যের অসীম সম্ভাবনার কথা—আঁভাগার্দ বা লিটল-ম্যাগধর্মী নিরীক্ষামূলক না হয়েও, মেইনস্ট্রিম গল্পকথনে থেকেও একজন লেখক কীভাবে থামতে পারেন প্রথাগত গল্প বলার ঠিক আগের দাগটায় গিয়ে, কিংবা সেই দাগ পেরিয়ে অন্য আকাশে উড়াল দিয়ে উঠে। এর ১১৬-টা অণুগল্পের (কয়েকটা গল্প মাত্র ১ বাক্যের আর সবচেয়ে বড়টা প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার) প্রত্যেকটা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন (দু-চারটা শুধু বাদে) এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, কিন্তু তারা সমগ্রের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে না মোটেই।
‘ফ্লাইটস্’ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় যে গল্পটা, সেটা পড়লে আপনার মনে পড়ে যাবে আন্তোনিওনির সিনেমা L’Avventura-র কথা। এক মহিলা এক দূর দ্বীপে স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়ে হাওয়া, নিখোঁজ। পুত্রের বয়স মাত্র তিন। দ্বীপটি ক্রোয়েশিয়ার এক ট্যুরিস্ট ডেসটিনেশন, এর প্রতিটি কোনা সবার চেনা, অতএব অকাণ্ড কিছু হবার কোনো সুযোগ নেই। মহিলার স্বামীকে তাই পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন আশ্বস্ত করেই চলেছে যে, সব ঠিক হয়ে যাবে, তোমার বউ-ছেলে ফেরত আসবে। পুলিশ স্টেশনে তাকে বিয়ার পান করতে দেয়া হয়, “যেন বা অফিসাররা আশা করছেন যে তাদের অসহায়ত্ব ঢাকা পড়ে যাবে ওই বিয়ারের সাদা ফোমের আড়ালে।” আমরা এ সময় অল্প অল্প টের পেতে শুরু করেছি যে এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছুটা টেনশন ছিল, সামান্য তুচ্ছ কোনো ঝামেলা ছিল, তবে তা বেড়াতে এসে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার মতো কিছু নয় মোটেই। স্বামী এবার স্ত্রীর ব্যাগ, স্যুটকেস সব হাতড়ানো শুরু করল, জিনিসগুলির তালিকা করা শুরু করল। “সে তার বউয়ের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে লাগল, একেকটি বস্তুর একেকটি আলাদা ছবি। সে ছবি তুলতে লাগল ধীরে, গম্ভীরভাবে, যতটা সম্ভব জুম ইন করে করে, ফ্ল্যাশ দিয়ে। তার একমাত্র আক্ষেপ যে এই ছোট ক্যামেরাটি ক্যামেরার নিজের শরীরের ছবি তুলতে পারে না।”
এরপর এই গল্পের দ্বিতীয় কিস্তিতে গিয়ে দেখা যায় ঘরে ফিরে এসেছে তার স্ত্রী ও পুত্র। তার স্ত্রী তাকে ভড়কে দিয়ে বলে যে, তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল, একটা বাগানে বসে ছিল, একটা ছোট পাথরের ঘর পেয়ে সেখানে ঘুমিয়েছিল, আঙুর খেয়ে থেকেছিল, আর তারা অনেক সাঁতার কেটেছে। কিন্তু তারা তো তিন দিন ধরে নিখোঁজ? তাহলে পানি কী করে পেয়েছে তারা? আমরা জানতে পারলাম তারা সমুদ্রের পানি খেয়ে বেঁচে থেকেছে।
স্বামীর কথা বলা হচ্ছে এবার: “ডিটেইল, ডিটেইলের ভার: সে আগে ডিটেইলকে সিরিয়াসলি নিতো না। এখন সে নিশ্চিত যে সবগুলি ডিটেইলকে যদি সে শক্তভাবে জোড়া দেওয়া একটা চেইনে গাঁথে—কারণ ও কার্যকে—তাহলে সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তাকে বসতে হবে চুপচাপ তার অফিসে গিয়ে, টেবিলে পাততে হবে একটা কাগজ, ভালো হয় কাগজটা বড় সাইজের হলে, যত বড় কাগজ হয় তত ভালো… আর তারপর ডট দিয়ে দিয়ে সব ডিটেইলকে ঢেলে সাজাতে হবে। কথা হচ্ছে, ওটাই তো সত্য।”
আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি এ-বইয়ের এমন অন্তত চল্লিশটা আজব গল্প পড়ে, বিশেষ করে মানবদেহ সম্পর্কিত (মৃত্যুর পরের মানবদেহ) এবং এয়ারপোর্ট বিষয়ক গল্পগুলি পড়ে। বিরাট সৃজনীক্ষমতা ওলগার, এবং তার দেখার চোখটা তির্যক, আর অতি অবশ্যই, হান্টকের মতোই, একইরকম সেবাল্ডিয়ান লিরিক ও লিরিকের ভেতরকার মন-কেমন-করা বিষণ্ণতা দিয়ে মোড়া। হান্টকের মতোই শেষে গিয়ে তোকারচুকেরও কাজ ওই একই—ধাক্কা দেওয়া, যে জায়গাটাতে তারা দু’জনেই আবার সেবাল্ড থেকে আলাদা। দু’জনকেই অভিনন্দন।









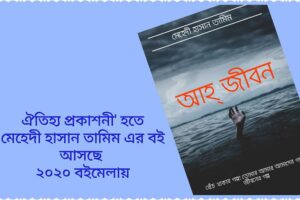

আপনার মন্তব্য লিখুন