ভাষান্তর: ফারুক মঈনউদ্দীন
(জাপানি কথাসাহিত্যিক হারুকি মুরাকামির জন্ম জানুয়ারি ১৯৪৯। বেশ কয়েকবছর ধরে তাঁর নাম নোবেল জল্পনায় এলেও ২০১৮ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের হ্রস্বতালিকায় তাঁর নাম থাকার কথাটি পাকাপোক্ত ছিল। কিন্তু সে বছরের পুরস্কারটি বাতিল করা হলে বিশ্বজুড়ে তাঁর ভক্তদের আবারও হতাশ হতে হয়। লেখক মুরাকামি যে একজন সিরিয়াস ম্যারাথন দৌড়বিদ, একথা তাঁর অনেক পাঠকেরই হয়তো জানা নেই। তাঁর বয়স যখন ৩৩, তখন প্রথম দৌড়বিদ হিসেবে অবতীর্ন হন তিনি। ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর তিনটি গ্রন্থ (হিয়ার দ্য উইন্ড সিং, পিনবল ১৯৭৩, অ্যা ওয়াইল্ড শিপ চেজ)। তারপর থেকে তিনি অগনিত স্বল্প পাল্লার দৌড়ে অংশগ্রহণ করার বাইরে মোট ২৬টি পূর্ণ ম্যারাথন দৌড়েছেন। তাঁর বয়স যখন ৪৭ তখন ৬২ মাইলের আলট্রা ম্যারাথন দৌড় সফলভাবে শেষ করতে পেরেছিলেন তিনি।
তাঁর স্মৃতিকথা হোয়াট আই টক অ্যাবাউট হোয়েন আই টক অ্যাবাউট রানিং-এর বাংলা অনুবাদ দৌড় বিষয়ে যত কথা প্রকাশ করছে প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ। নিচের অংশটি প্রকাশিতব্য বইয়ের অংশবিশেষ।)
আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে আমেরিকান রানার্স ওয়ার্ল্ড সাময়িকী আমার ছবি তোলার জন্য আসে। গ্রেগ নামের এক তরুণ ক্যামেরাম্যান ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসে সারা দিন কাটিয়ে আমার ছবি তোলে। উৎসাহী ছেলেটা প্রায় এক ট্রাকভর্তি যন্ত্রপাতি প্লেনে চাপিয়ে নিয়ে আসে কাউয়াই পর্যন্ত। এরা আমার সাক্ষাৎকার আগেই নিয়ে রেখেছিল, ছবিগুলো সেই সাক্ষাৎকারের সাথে দেওয়ার জন্য তোলা। ম্যারাথন দৌড়ায় এ রকম ঔপন্যাসিক আপাতত খুব বেশি নেই (আছে হয়তো কয়েকজন, কিন্তু অনেক নয়)। এই ম্যাগাজিনটা একজন ‘দৌড়ানো ঔপন্যাসিক’ হিসেবে আমার জীবন নিয়ে আগ্রহী ছিল। রানার্স ওয়ার্ল্ড আমেরিকান দৌড়বিদদের কছে খুব জনপ্রিয় পত্রিকা, তাই ভাবি, আমি এবার নিউইয়র্ক গেলে বহু দৌড়বিদ আমাকে ‘হাই’ বলবেন। এই ভাবনা আমাকে আরও উদ্বেগে ফেলে দেয় যাতে আমি ম্যারাথনে একটা বাজে ফল না করি।
ফিরে যাওয়া যাক ১৯৮৩ সালে। এক স্মৃতিময় সময় ছিল সেটা, যখন ডুরান ডুরান১ এবং হল ও ওটস২ একের পর এক হিট গান বের করে যাচ্ছিলেন।
সে বছর জুলাই মাসে আমি গ্রিসে যাই এবং এথেন্স থেকে ম্যারাথন শহর পর্যন্ত একা একা দৌড়াই। এটা ছিল যুদ্ধের আসল দূতের উল্টো পথ, যেটা ম্যারাথন থেকে শুরু হয়ে এথেন্স পর্যন্ত যায়। আমি ঠিক করেছিলাম আমি উল্টো পথে যাব, কারণ, হিসাব করেছিলাম যে ভোরে ভিড় শুরু হওয়ার আগেই (এবং বাতাস খুব বেশি দূষিত হওয়ার আগে) এথেন্স থেকে শুরু করে শহর ছেড়ে ম্যারাথনের দিকে যাব, যাতে গাড়ির ভিড় এড়ানো যায়। এটা কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা নয়, তাই স্বভাবতই আমার জন্য কোনো ফিরতি গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না।
একা একা ছাব্বিশ মাইল দৌড়ানোর জন্য কেন সুদূর এথেন্স পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমি? গ্রিসের ওপর একটা ভ্রমণকাহিনি লেখার জন্য একটা পত্রিকা আমাকে অনুরোধ করেছিল। সেটা ছিল গণমাধ্যমের জন্য গ্রিক সরকারের ট্যুরিজম বোর্ড-সংগঠিত আনুষ্ঠানিক একটা সফর। আরও অনেক পত্রিকা এই সফরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সফরসূচির মধ্যে ছিল সেখানকার ধ্বংসাবশেষ দেখা, ইজিয়ান সাগরে নৌভ্রমণ ইত্যাদি, কিন্তু এসব শেষ হওয়ার পর যত দিন ইচ্ছে থেকে আমার যা খুশি করার জন্য ছিল ওপেন টিকিট। এ-জাতীয় প্যাকেজ ভ্রমণ আমাকে খুব টানে না, কিন্তু পরে নিজের মতো করে থাকার ব্যবস্থাটা আমার পছন্দ হয়। গ্রিস হচ্ছে আদি ম্যারাথনের জন্মস্থান, নিজ চোখে সেটা দেখার জন্য আমার ছিল দুর্মর আগ্রহ। আমি হিসাব করি যে অন্তত এটার এক অংশ আমি নিজে দৌড়াতে পারব। আমার মতো নতুন শুরু করা একজন দৌড়বিদের জন্য এটা ছিল এক উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা।
আমি ভাবি, আরে! মাত্র এক অংশ কেন? পুরো দূরত্বটা দৌড়াই না কেন?
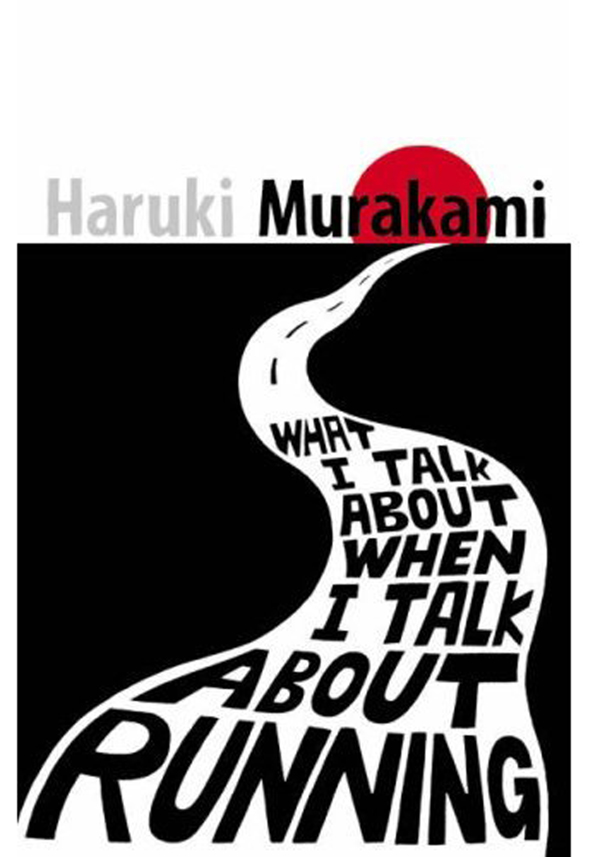
আমি যখন পত্রিকাটির সম্পাদকদের এই বিষয়টা বলি, তাঁরা পছন্দ করেন। এভাবেই আমি চুপচাপ নিজে নিজে আমার প্রথম পূর্ণ ম্যারাথনটি (কিংবা প্রায় তার কাছাকাছি) দৌড়াতে পেরেছিলাম। কোনো দর্শক নেই, সমাপ্তিরেখায় কোনো ফিতা নেই, পথে পথে নেই মানুষের আন্তরিক সহর্ষ চিৎকার। এসবের কিছুই নেই। ওটা আদি ম্যারাথনের পথ বলে এটাই ছিল যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশি আর কী চাই আমার?
আসলে এথেন্স থেকে ম্যারাথন পর্যন্ত সোজা দৌড়ালে সেটা আনুষ্ঠানিক ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব হয় না, যা নির্দিষ্ট করা আছে ২৬.২ মাইল। এই পথটা এক মাইল কম। কয়েক বছর পর একটা আনুষ্ঠানিক ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করার পর জানতে পারি এটা, যেটা মূল রাস্তা ধরে ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এথেন্স অলিম্পিকের টেলিভিশন সম্প্রচার যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, দৌড়বিদেরা ম্যারাথন ছাড়ানোর পর এক জায়গায় এসে বাম দিকের একটা পার্শ্বরাস্তা ধরে কিছু স্বল্পপরিচিত ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে দৌড়ান, তারপর আবার মূল সড়কে উঠে আসেন। এভাবেই বাড়তি দূরত্বটা দৌড়ানো হয়। সেবার বিষয়টা আমার জানা ছিল না, তাই ভেবেছিলাম, এথেন্স থেকে ম্যারাথন পর্যন্ত দৌড়ালে ২৬.২ মাইল হবে। আসলে দূরত্বটা ছিল পঁচিশ মাইল। তবে এথেন্সের ভেতর আমি কয়েকটা বাঁক নিয়েছিলাম বলে আমার সাথের গাড়িতে থাকা অডোমিটার দেখাচ্ছিল যে গাড়িটা ছাব্বিশ মাইল চলেছে, তাই আমার ধারণা, একটা পুরো ম্যারাথনের খুব কাছাকাছি দৌড়েছি আমি। অবশ্য এত দিন পর এতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না।
আমি যেবার দৌড়াই, তখন এথেন্সে ছিল গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়। যাঁরা ওখানে থাকেন তাঁরা জানেন গরমটা কেমন অবিশ্বাস্য সে সময়। বাধ্য না হলে বিকেলে বাইরে যাওয়াটা পরিহার করে চলে স্থানীয়রা। সে সময় তারা কিছুই করে না, কেবল ছায়ার নিচে ঠান্ডায় থেকে শক্তিটা ধরে রাখে। সূর্য ডুবে গেলেই তবে রাস্তায় বের হয় ওরা। গ্রীষ্মের বিকেলে যাদের বাইরে চলাফেরা করতে দেখা যায়, তারা ট্যুরিস্ট। সে সময় এমনকি কুকুরগুলোও একটুও নড়াচড়া না করে ছায়ার নিচে শুয়ে ঘুমায়। ওগুলো সত্যিই বেঁচে আছে কি না, বোঝার জন্য অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে হয়। এমনই গরম। ওরকম গরমে ছাব্বিশ মাইল দৌড়ানো পাগলামো ছাড়া কিছু নয়।
আমি যখন গ্রিকদের এথেন্স থেকে ম্যারাথন পর্যন্ত একা দৌড়ানোর পরিকল্পনার কথা বলি, তাদের সবাই একই কথা বলে: ‘এটা পাগলামি। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এটা ভাবতেই পারবে না।’ আসার আগে আমারও কোনো ধারণাই ছিল না গ্রীষ্মে এথেন্সে কেমন গরম পড়ে, তাই এ ব্যাপারে বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলাম। আমার যা করার ছিল, সেটা হচ্ছে ছাব্বিশ মাইল দৌড়ানো, কেবল দূরত্বের ব্যাপারটা মাথায় ছিল আমার, তাপমাত্রার বিষয়টা কখনোই মনে আসেনি। এথেন্সে পৌঁছার পর এমন গনগনে গরম দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। তাঁরা যে ঠিক বলেছেন, বুঝতে পারি সেটা। পাগল ছাড়া এই কাজ কেউ করবে না। তবু আমি মূল ম্যারাথন কোর্সটা দৌড়ে তার ওপর একটা লেখা লিখব, এই প্রতিশ্রুতিতে বর্ণিল মনোভাব নিয়ে সুদূর গ্রিস পর্যন্ত ছুটে এসেছি। এ অবস্থায় কোনোভাবেই পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। গরমে শেষ হয়ে যাওয়া থেকে কীভাবে বাঁচা যায়, সেই ভাবনায় কঠিনভাবে মাথা খাটাই আমি। শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধি মাথায় আসে যে খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই এথেন্স ছেড়ে যেতে হবে, যাতে সূর্য ওপরে ওঠার আগেই ম্যারাথনে পৌঁছে যাওয়া যায়। যত দেরি হবে গরম তত বেশি হবে। এটা সূর্যকে পরাস্ত করার প্রতিযোগিতায় হুবহু সেই রান মেলোস!৩ গল্পের মতো দাঁড়াচ্ছে।
ম্যাগাজিনটার ফটোগ্রাফার মাসাও কাগেয়ামা তাঁর গাড়ি নিয়ে দৌড়ানোর সময় আমার সাথে সাথে ছিলেন। সে সময় আমার ছবি তোলা হয়। এটা কোনো সত্যিকার প্রতিযোগিতা ছিল না, তাই ঘাটে ঘাটে জলপানেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণে আমাকে মাঝেমধ্যে ভ্যান থেকে পানি খাওয়ার জন্য থামতে হয়। গ্রিসের গ্রীষ্ম সত্যিই নির্মম, সেটা জানতাম বলে পানিশূন্য হয়ে না পড়ার জন্য আমাকে সাবধান থাকতে হবে।
দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখে কাগেয়ামা অবাক হয়ে আমাকে জিগ্যেস করে, ‘জনাব মুরাকামি, আপনি নিশ্চয়ই পুরো পথ দৌড়ানোর কথা ভাবছেন না?’
‘অবশ্যই পুরো রাস্তা। সে জন্যই তো এখানে এসেছি আমি।’
‘সত্যিই? কিন্তু আমরা যখন এ-জাতীয় কাজে আসি, আমরা পুরো পথ সাথে সাথে যাই না। আমরা কেবল কিছু ছবি তুলি এবং তাঁরাও পুরো রাস্তা দৌড়ান না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই পুরো দূরত্ব দৌড়াবেন?’
কখনো কখনো দুনিয়া আমাকে বিপাকে ফেলে। আমার বিশ্বাস, লোকজন আমার সাথে সে রকম কিছু করবে না।
সে যা-ই হোক, আমি ভোর সাড়ে পাঁচটায় স্টেডিয়াম থেকে যাত্রা শুরু করে ম্যারাথন যাওয়ার রাস্তা ধরি, এই স্টেডিয়ামটা ২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে ব্যবহৃত হয়েছিল। ওটা ছিল একমাত্র মূল হাইওয়ে। গ্রিসে দৌড়ালে বোঝা যায়, ওদের রাস্তাগুলো অন্য রকম করে বাঁধানো। নুড়িপাথরের বদলে ওরা মার্বেল পাথরের গুঁড়া ব্যবহার করে, এতে রাস্তাটা সূর্যের আলোতে চকচক করে এবং বেশ পিচ্ছিল হয়। বৃষ্টি হলে খুব সাবধান থাকতে হয়। বৃষ্টি না হলেও জুতোর তলা থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়, পায়ে টের পাওয়া যায় রাস্তা কেমন মসৃণ।
এথেন্স-ম্যারাথন দৌড় নিয়ে ম্যাগাজিনটায় যে লেখাটা আমি লিখেছিলাম, নিচে সেটার সংক্ষেপিত ভাষ্য দিলাম।
*
সূর্য ওপরে উঠছে। এথেন্স শহরের ভেতর দৌড়ানো খুব কঠিন। স্টেডিয়াম থেকে হাইওয়েতে ওঠার মুখটা প্রায় তিন মাইল, এই পথে অনেকগুলো ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি পড়ে, সেগুলোর কারণে আমার গতি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। অনেক জায়গায় নির্মাণকাজ এবং ডবল পার্ক করে রাখা গাড়িগুলো রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে, তাই আমাকে রাস্তার মাঝখানে নেমে আসতে হয়। ভোরবেলায় তীব্র গতিতে ছুটে আসা গাড়িগুলোর কারণে এখানে দৌড়ানো বিপজ্জনক।
ম্যারাথন অ্যাভিনিউতে ঢোকার পরপরই সূর্য উঠতে থাকে, রাস্তার বাতিগুলো সাথে সাথে নিভে যায়। গ্রীষ্মের সূর্য ঠিক যে সময়ে পৃথিবীকে শাসন করে, সেই সময়টা দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোকজন বাসস্টপে পৌঁছা শুরু করেছে। গ্রিকরা দুপুরের পর দিবানিদ্রা দেয়, তাই তারা কাজে যায় বেশ ভোরে। তাদের সবাই আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের কেউ আগে কখনো একজন প্রাচ্যদেশীয়কে ভোরবেলায় এথেন্সের রাস্তায় দৌড়াতে দেখেছে, এমনটা মনে হয় না। এথেন্স দিয়ে শুরু করার জন্য বহু দৌড়বিদ যে এখানে আসে, তেমন নয়।
চার মাইল দৌড়ানোর পর জামা খুলে ফেলতে হয়, ফলে কোমর থেকে আমার ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি। সব সময়ই কোনো জামা না পরেই দৌড়াই আমি, তাই জামা খুলে ফেলার পর আরাম লাগে (যদিও পরে ভয়ংকর রকম রোদপোড়া হয়েছিলাম)। আট মাইল পর্যন্ত ক্রমাগত উঠে যাওয়া একটা ঢাল বেয়ে দৌড়াই আমি। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। ঢালের মাথায় ওঠার পর মনে হলো আমি শেষ পর্যন্ত শহর ছাড়িয়েছি। কিছুটা স্বস্তি পাই, কিন্তু একই সাথে দেখি, এখান থেকে ফুটপাত উধাও, তার বদলে কেবল রাস্তার ওপর একটা সরু পথ আলাদা চিহ্নিত করে সাদা রেখা টানা। ভিড়ের সময় শুরু হয়েছে, গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গেছে রাস্তায়। বড় বড় বাস-ট্রাক প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে আমার ঠিক পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে ছুটে যাচ্ছিল। ম্যারাথন অ্যাভিনিউ নামের রাস্তার সাথে ইতিহাসের খুব আবছা একটা সংযোগের থাকলেও এটা মূলত যানবাহনের জন্য একটা সাধারণ হাইওয়ে।
এক জায়গায় পৌঁছে আমি প্রথমবারের মতো একটা মরা কুকুর দেখতে পাই। বড় একটা বাদামি কুকুর। বাইরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। কেবল রাস্তার মাঝখানে শুয়ে ছিল যেন। বুঝতে পারি একটা বেওয়ারিশ কুকুর, মাঝরাতে কোনো ছুটন্ত গাড়ি ধাক্কা দিয়ে গেছে। শরীরটা তখনো গরম ছিল, তবে মরা বলে মনে হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল যেন ঘুমাচ্ছে। ট্রাক ড্রাইভাররা ওটার দিকে একপলকও না তাকিয়ে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।
অল্প দূর গিয়ে আরেকটা বিড়াল দেখতে পাই, কোনো গাড়ি পিষে দিয়ে গেছে। শরীরটা সম্পূর্ণ থ্যাঁতলানো, যেন কোনো ভুল আকৃতির শুকানো পিৎজা। বহু আগেই গাড়িচাপা পড়া।
আমি যে রাস্তার কথা বলছি, সেটা এ রকমই।
এ পর্যায়ে এসে আমি ভাবতে শুরু করি সুদূর টোকিও থেকে উড়ে এসে কেন আমাকে এই নিরানন্দ মহাসড়কে দৌড়াতে হচ্ছে। আমার করার মতো নিশ্চয়ই অন্য অনেক কাজ ছিল। ম্যারাথন অ্যাভিনিউতে যে বেচারা প্রাণীগুলো এক দিনে প্রাণ দিল, সেগুলোর মধ্যে তিনটা কুকুর ও এগারোটা বিড়াল। সব গুনেছি আমি, মন খারাপ হয়ে যায়।
আমি দৌড়ে চলি। সূর্য অবিশ্বাস্য গতিতে আকাশে উঠে নিজেকে পূর্ণ প্রকাশিত করে। তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি। ঘাম হওয়ার সময়টাও পাচ্ছে না, বাতাস এত শুকনো যে ঘাম হওয়ামাত্র উবে যাচ্ছে, ফেলে যাচ্ছে সাদা লবণের স্তর। ঘামের ফোঁটা বলার মতো একধরনের প্রকাশভঙ্গি আছে, কিন্তু এখানে ফোঁটা তৈরি হওয়ার আগেই ঘাম উধাও হয়ে যাচ্ছে। আমার সারা শরীরে লেগে থাকা লবণের হুল বিঁধতে থাকে। ঠোঁট চাটলে মনে হচ্ছিল যেন অ্যানচভি৪ মাছের ভর্তা। একটা বরফশীতল বিয়ারের স্বপ্ন দেখতে থাকি আমি, এমন ঠান্ডা, যেন শরীর পোড়ায়। আশপাশে কোনো বিয়ারের ব্যবস্থা নেই, তাই প্রতি তিন মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বের পরপর পত্রিকা সম্পাদকের গাড়ি থেকে পানি খাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। আগে কখনোই দৌড়ানোর সময় এত বেশি পানি খাইনি আমি।
বেশ ভালো লাগে এখন। অনেক শক্তি অবশিষ্ট রয়েছে শরীরে। আমার ক্ষমতার প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহার করে দৌড়াই, তবুু একটা সম্মানজনক কদম বজায় রাখতে পারি। কিছুদূর পরপর রাস্তা চড়াই হচ্ছে, তার পর উতরাই। শহর পেছনে ফেলে আসি আমি, তারপর শহরতলি এবং ক্রমে আরও গ্রাম্য এলাকায় ঢুকি। ‘নেয়া মাকরি’ নামের ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, বুড়ো লোকজন ক্যাফের বাইরে বসে ছোট ছোট কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চুপচাপ আমাকে দৌড়ে যেতে দেখছেন। যেন ইতিহাসের অচল পাতা থেকে কোনো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা।
প্রায় সতেরো মাইলের মাথায় একটা ঢাল, সেটা পার হওয়ার পর আমি একঝলক ম্যারাথন পাহাড়ের দেখা পাই। বুঝতে পারি দৌড়ের দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হয়েছে। মনে মনে হিসাব করে বুঝতে পারি এই গতিতে গেলে সাড়ে তিন ঘণ্টায় শেষ করতে পারব। কিন্তু সবকিছু সে রকম ঠিকভাবে হয় না। উনিশ মাইল পার হওয়ার পর সমুদ্রের দিক থেকে বিপরীতমুখী বাতাস শুরু হয়, ম্যারাথনের যত কাছাকাছি পৌঁছাই, বাতাস তত তীব্রতর হতে থাকে। সেই বাতাস এমনই তীব্র ছিল যে গায়ে হুল ফোটাতে থাকে। মনে হচ্ছিল একটু ঢিলা দিলেই বাতাস পেছনে উড়িয়ে নিয়ে যাবে আমাকে। রাস্তাটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করলে আমি হালকাভাবে সমুদ্রের ঘ্রাণ পাই। ম্যারাথনে যাওয়ার একটিইমাত্র রাস্তা, আর সেটা রুলারের মতো সোজা। এই জায়গায় এসে আমি সত্যিকার অবসন্ন বোধ করতে শুরু করি। কতখানি পানি খেয়েছি, সেটা কিছুই নয়, কয়েক মিনিট পরই আমার আবার তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছিল। একটা ভালো ঠান্ডা বীয়ার হলে চমৎকার হতো।

নাহ্, বিয়ারের কথা ভুলে যাই। রোদের কথাও। ভুলে যাই বাতাসের কথাও। যে লেখাটা লিখতে হবে, সেটার কথাও ভুলে যাই। কেবল সামনে বাড়ার কথা ভাবি, একটার পর আরেকটা কদম। এটাই এখন একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।
বাইশ মাইল অতিক্রম করি আমি। আগে কখনোই বাইশ মাইলের বেশি দৌড়াইনি, তাই এর পর হচ্ছে অজ্ঞাত ভুবন। আমার বামে ঊষর পাহাড়ের বন্ধুর একটা সারি। কে বানিয়েছে ওটা? হাতের ডানে জলপাই গাছের অন্তহীন বিস্তার। সবকিছুই মনে হচ্ছে সাদা ধুলোয় ঢাকা। সমুদ্রের দিক থেকে আসা বাতাস হাল ছাড়ে না কিছুতেই। এই বাতাসের হয়েছেটা কী? তাকে এমন তীব্রভাবে বইতে হবে কেন?
বাইশ মাইলের কাছাকাছি এসে সবকিছু অপছন্দ হতে শুরু হয় আমার। যথেষ্ট হয়েছে! তলানিতে নেমে এসেছে আমার ক্ষমতা, আর দৌড়াতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় শূন্যতার মধ্যে একটা গাড়ি চালাচ্ছি। কিছু একটা পান করতেই হবে আমাকে, কিন্তু মনে হচ্ছে এখন পানি খাওয়ার জন্য থামলে, তাহলে আর দৌড়াতে পারব না। তেষ্টায় মরে যাচ্ছি, কিন্তু পানি খাওয়ার শক্তিটুকু আর অবশিষ্ট নেই। এসব ভাবনা আমার মনে যখন হালকাভাবে ওড়াউড়ি করছিল, ক্রমে রেগে উঠছিলাম আমি। রাগ হচ্ছিল রাস্তার পাশের খালি জমিতে মনের আনন্দে ঘাস চিবানো মেষগুলোর ওপর, গাড়ির ভেতর বসে আমার ছবি তুলতে থাকা ফটোগ্রাফারের ওপর। শাটারের শব্দ আমার স্নায়ুতে ঘষা দিচ্ছিল। এতগুলো মেষ কার দরকার পড়ে? কিন্তু শাটার টেপা হচ্ছে ফটোগ্রাফারের কাজ, যেমন মেষের কাজ হচ্ছে ঘাস চিবানো, সুতরাং কারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই। তবু সবকিছু আমাকে সীমাহীনভাবে বিরক্ত করতে থাকে। আমার চামড়ার ওপর সাদা ফুসকুড়ি উঠতে থাকে। ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠছে। এই গরমের সমস্যাটা কী?
পঁচিশ মাইলের চিহ্ন পার হই আমি।
‘আর মাত্র এক মাইল। দৌড়াতে থাকুন,’ গাড়ি থেকে ফটো সম্পাদক সোল্লাসে চিৎকার করে বলে। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, তোমার পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু বলি না। নগ্ন সূর্য গনগনে তাপ ছড়াচ্ছিল। এখন মাত্র সকাল নয়টা পেরিয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমি যেন চুলার ভেতর বসে আছি। চোখের মধ্যে ঘাম ঢুকে যাচ্ছে। লবণ কামড় দেয় চোখে, কিছুক্ষণের জন্য কিছুই দেখতে পাই না। হাত দিয়ে ঘাম মুছে ফেলি, কিন্তু হাত আর মুখও লবণাক্ত, আর তাতে চোখ আরও জ্বালা করে ওঠে।
গ্রীষ্মের লম্বা ঘাসের পেছনে গ্রামে ঢোকার মুখে সমাপ্তিরেখাটা কোনোরকমে দেখতে পাই আমি, গ্রামটির সমনামী ম্যারাথন স্মারকস্তম্ভ। ওটা এত দ্রুত সামনে চলে আসে যে প্রথমে আমি নিশ্চিত ছিলাম না, ওটা আসলেই সমাপ্তিরেখা ছিল কি না? তবু ওটা দেখে আমি খুশি হই, এটা নিয়ে কোনো কথা নেই, কিন্তু এই আকস্মিকতা কোনো কারণে আমাকে প্রায় পাগল করে ফেলে। যেহেতু দৌড়ের শেষ পর্যায় ছিল ওটা, যত দ্রুত সম্ভব মরিয়া একটা চেষ্টা করতে পারি আমি, কিন্তু আমার দুই পায়ের ছিল নিজস্ব মন। ভুলেই গিয়েছিলাম কীভাবে শরীর নাড়ানো যায়। পেশিগুলোর এমন অবস্থা ছিল যে মনে হয় কোনো জংধরা রেঁদা দিয়ে ওগুলোকে চেঁছে দেওয়া হয়েছে।
আসে সমাপ্তিরেখা।
শেষ পর্যন্ত পৌঁছাই আমি। আশ্চর্যের বিষয়, আমার ভেতর পরিপূর্ণতার কোনো অনুভূতি আসে না। আমার একমাত্র অনুভূতি ছিল একটা পরম স্বস্তি যে আমাকে আর দৌড়াতে হবে না। আমি একটা গ্যাস স্টেশনে গিয়ে ওদের কলের পানি দিয়ে অতি উত্তপ্ত শরীরকে ঠান্ডা করি, শরীরে লেগে থাকা লবণ ধুয়ে ফেলি। লবণে ঢাকা আমি যেন যথার্থ এক মানব-লবণখনি। গ্যাস স্টেশনের বৃদ্ধ লোকটা যখন জানতে পারেন যে আমি কী করেছি, তিনি টবে লাগানো গাছ থেকে কিছু ফুল কেটে নিয়ে এসে আমাকে একটা ফুলের তোড়া উপহার দেন। ‘বিরাট কাজ করেছেন আপনি,’ বলে তিনি হাসেন। ‘অভিনন্দন।’ বিদেশিদের এই সব ছোট ছোট উদারতায় আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। ম্যারাথন ছোট ঘরোয়া একটা গ্রাম, চুপচাপ, শান্তিপূর্ণ। আমার মাথায় আসে না কয়েক হাজার বছর আগে কীভাবে এখানকার সমুদ্রতীরে প্রাণঘাতী এক যুদ্ধে গ্রিকরা পারসিকদের হারিয়ে দিয়েছিল। আমি গ্রামের এক ক্যাফেতে বসে ঢকঢক করে ঠান্ডা অ্যামস্টেল বিয়ার খাই। স্বাদটা চমৎকার লাগে, কিন্তু দৌড়ানোর সময় আমি যে রকম বিয়ারের কথা কল্পনা করছিলাম তার মতো নয়। বাস্তব দুনিয়ার কিছুই চেতনা হারিয়ে ফেলার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া একজনের মায়াবিভ্রমের মতো সুন্দর হয় না।
এথেন্স থেকে ম্যারাথন পর্যন্ত দৌড়ে আমার সময় লাগে তিন ঘণ্টা একান্ন মিনিট। খুব বিরাট কিছু নয়, তবু আমি অন্তত পুরোটা পথ একা দৌড়াতে পেরেছি, আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল জঘন্য ট্রাফিক, অকল্পনীয় গরম আর মারাত্মক জলপিপাসা। মনে হয় আমি যা করেছি, তার জন্য আমার গর্বিত হওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই যায় আসে না। এখন আমাকে খুশি করে এই ভাবনা যে আমাকে আর এক কদমও দৌড়াতে হবে না।
উফ!—আমাকে আর দৌড়াতে হবে না।
*
ছাব্বিশ (প্রায়) মাইল দৌড়ানোর অভিজ্ঞতা আমার এবারই প্রথম। সুখের বিষয়, এ রকম ক্লান্তিকর অবস্থায় এটাই ছিল আমার শেষ দৌড়। একই বছরের ডিসেম্বরে আমি হনুলুলু ম্যারাথনে দৌড়াই বেশ সম্মানজনক সময়ের মধ্যে। হাওয়াইও গরম, কিন্তু এথেন্সের ধারেকাছেও নয়। সে হিসেবে হনুলুলুরটা ছিল আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক ম্যারাথন। তার পর থেকে আমার রেওয়াজ ছিল বছরে একটা পূর্ণ ম্যারাথন দৌড়ানো।
সেবারে গ্রিসে দৌড়ানোর পর আমি যে লেখাটা লিখেছিলাম, প্রায় বিশ বছর পর সেটা আবার পড়ে মনে হলো, পরবর্তী সময়ে আমি যতগুলো ম্যারাথন দৌড়েছি, সেগুলোর অভিজ্ঞতা প্রথমবার ছাব্বিশ মাইল দৌড়ানোর মতোই। এখনো পর্যন্ত আমি যখন কোনো ম্যারাথন দৌড়াই, আমার মন ঠিক একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। উনিশ মাইল পর্যন্ত আমি নিশ্চিতভাবে ভালো দৌড়াই, কিন্তু বাইশ মাইলের পর আমার জ্বালানি শেষ হয়ে আসে এবং সবকিছুর ওপর বিরক্ত হতে থাকি আমি। শেষে গিয়ে আমার নিজেকে মনে হয় তেল শেষ হয়ে আসা গাড়ির মতো। কিন্তু শেষ হওয়ার পর কিছুদিন গেলে আমি সব যন্ত্রণা ও দুর্দশার কথা ভুলে যাই এবং পরিকল্পনা করতে থাকি পরেরবার কীভাবে আরও ভালো দৌড়ানো যায় । মজার ব্যাপার হচ্ছে কতবারের অভিজ্ঞতা আমার ঝুলিতে আছে, কতটা বয়স হয়েছে আমার —এসবে কিছুই যায় আসে না, এটা কেবলই আগের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি।
আমার মনে হয় নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো কোনো ভিন্নতা আনতে দেয় না। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হতে হলে যা করতে হয়, সেটা হচ্ছে নিজেকে ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে রূপান্তর—অথবা হয়তো বিকৃত করা—আর সেই প্রক্রিয়াকে নিজের ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত করা।
অনুবাদকের টীকা:
১. ডুরান ডুরান: ১৯৭৮ সালে বার্মিংহামে গঠিত একটা নতুন ধারার ব্যান্ড।
২. হল ও ওটস: হল অ্যান্ড ওটস আমেরিকান শিল্পীযুগলের সংক্ষিপ্ত নাম। ড্যারিল হল হচ্ছেন প্রধান ভোকালিস্ট এবং জন ওটস গিটারিস্ট।
৩. রান মেলোস: জাপানি লেখক ওসামু দাজাইর লেখা ১৯৪০ সালে প্রকাশিত স্কুলপাঠ্য একটা জাপানি ক্ল্যাসিক গল্প। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে লেখা গল্পটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে অবিচল বন্ধুত্ব। অনেক কষ্ট সহ্য করেও মূল চরিত্র মেলোস তার বন্ধুর জীবন রক্ষা করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং শেষ পর্যন্ত তার এই প্রচেষ্টার পুরস্কার সে পায়।
৪. অ্যানচভি: হেরিং-জাতীয় ছোট মাছ।











আপনার মন্তব্য লিখুন